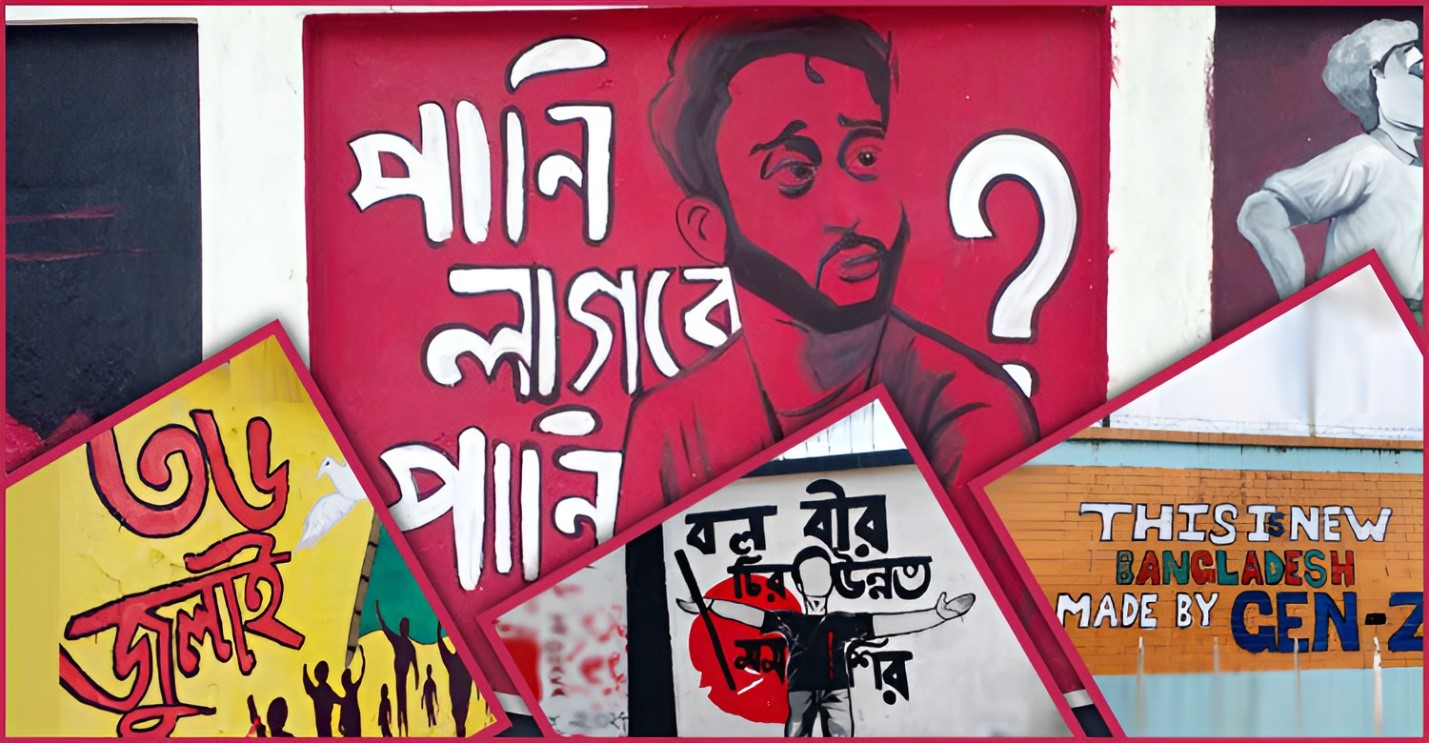আঠারো শতাব্দি থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো দখলকৃত কলোনিগুলোয় ক্রমাগতভাবে তাদের ক্ষমতাকে দৃশ্যমান করে তোলার তাগিদে শুধু আচার অনুষ্ঠান কিংবা রঙ্গমঞ্চ প্রদর্শন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং দাপ্তরিক কায়দায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অফিসিয়াল প্রক্রিয়া অনুসরন করেই অনেক অঞ্চলে/ভুখন্ডে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা ট্রাডিশন এবং নিত্য নতুন বিষয়কে নয়াভাবে সংজ্ঞায়ন ও শ্রেনীবিভাগ করে, পাবলিক প্রাইভেট পরিসরকে আলাদা করে, লেনদেনের কার্যবিবরনী সংরক্ষণ করার নতুন পদ্ধতি আনে। যেমনঃ সম্পত্তির বিক্রয় সংক্রান্ত নিয়মকানুনকে লিপিবদ্ধ করা, এছাড়া আদমশুমারি পরিচালনা ও জনসংখ্যকে শ্রেনীবিভাগ করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টারের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া এবং দলিলপত্র ও ভাষাকে প্রমিতকরণ করার মধ্যে দিয়ে সবকিছুর নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া। রাষ্ট্র তখন কোন একটি ট্রাডিশন এবং কাজকে বৈধ হিসেবে অনুমতি দেয়ার পাশাপাশি অন্য আরেকটিকে বেআইনী বা অনৈতিক বলে বাতিল করতে থাকে। গণশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিত্য নতুন বিধি বিধান ও তাহযীব সম্পর্কে পরিচয়করণ ও সেসব কীভাবে চর্চা করতে হবে ও মানতে হবে তা নিয়ে রাষ্ট্র নিজেই প্রচারণা চালায়। স্কুলগুলো মুলত সিভিলাইজিং (অর্থাৎ জনগোষ্ঠীকে সভ্যতার আদলে গড়ে তোলার) প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাজির হয় এবং নৈতিকতার উৎপাদন ও কার্যকরী নাগরিক গড়ে তোলার কাজ করতে শুরু করে। এভাবেই ইতিহাস, ভুখন্ড ও সমাজের প্রাকৃতিক প্রতিমুর্তি হিসেবে জাতি রাষ্ট্র হাজির হয়।
এইসব জাতিরাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শুরুতেই পুর্বের ব্যবস্থাকে পুনরায় নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রন, লিপিবদ্ধকরন ও প্রতিনিধিত্ব করার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তো এই ক্ষেত্রে বিশাল পরিমান তথ্যের ডকুমেন্টেশান বানানো হয়। আর এই ডকুমেন্টেশানের কারনেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা তাদের জন্য সহজ হয়ে উঠে। কমিশনের তৈরি করা তদন্ত প্রতিবেদন, বিভিন্ন তথ্যের সংকলন, সংরক্ষণ এবং অর্থ, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, অপরাধ, শিক্ষা, পরিবহন, কৃষি, এবং শিল্পের পরিসংখ্যানগত তথ্য উপাত্তের প্রকাশনা তৈরি করা হয়। এই তৈরি তথ্যগুলো ততটাই দরকারি ঠিক যতটা সংস্কৃত পুস্তক ব্যাখা করার জন্য তাফসির শাস্ত্রের উপর দক্ষতার দরকার হয়।
আধুনিক ইউরোপ শুরুর দিকে সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে অপ্রত্যাশিত উন্নয়ন করে। এই অভুতপুর্ব উন্নয়নের বদৌলতেই মুসলিম রাজ্যগুলিকে দখল করে নিতে সক্ষম হয়। প্রথমে আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম উপকুল পরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এরপরে অনান্য অঞ্চলকে দখলে নেয়। উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে ইউরোপ কতিপয় অগুরুত্বপুর্ণ ও ক্ষুদ্র আয়তনের মুসলিম জনপদ বাদে বিশ্বের নয় দশমাংশ ভুখন্ডকে দখল করে নেয়। যদিও ষোড়শ শতাব্দির এই বিজয়গুলি ধর্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠার নামে ছিল, ঠিক তাদের পূর্বসুরিদের ক্রুসেডের মত, কিন্ত এর পেছনের উদ্দেশ্য ছিল পরাজিতদের সম্পদ লুন্ঠন করা। যেহেতু বস্তুগত মুনাফা ছিল মুল উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপনিবেশায়নের স্বভাবগত উদ্দেশ্য মুলত এটাই থাকে, যার কারণে দখলকৃত ভুখন্ডকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও ব্যবসা বানিজ্যের অধীনস্ত করার জন্য তাদের আইন কানুনকে বদলিয়ে ফেলে। উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোর আইনি ইতিহাস ঘেটে দেখলেই এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়। এমনকি কয়েক শতাব্দি জুড়ে ইসলামের শাসনের অধীনে যেসব অঞ্চল ছিল সেসব জায়গাতেও আইনের ক্ষেত্রে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। একইভাবে আমরা দেখব যে উপনিবেশিত অঞ্চলের স্থানীয় আইনি কাঠামোর সাথে পশ্চিমা আইনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি বিধান বিষয়ক। আর ঐসব বিধি-বিধানের আলোকেই উপনিবেশিত বাজারকে ইউরোপীয়ান আইন অনুযায়ী ব্যবসা বাণিজ্য করার জালে আটকানো হয়।
প্রথমে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি বিধানের কার্যক্রম সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে তারা উপনিবেশগুলোতে পা রাখার প্রাথমিক ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করার পরপরই ইউরোপীয় পেনাল কোডের প্রত্যাবর্তন করে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ফলে যে নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে তার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে ঢেলে সাজানো হয়। আমি এই ঘটনাকে রাজনৈতিক হিসেবে সাব্যস্ত করি। কারণ, বিশেষ করে পরোক্ষ উপনিবেশবাদের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক কার্যক্রম পদ্ধতিগতভাবে এবং আগ্রাসনমুলকভাবে রাজনৈতিক মাকসাদকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছে। তাই উপনিবেশগুলোতে পেনাল কোডের প্রত্যাবর্তন করা রাজনৈতিক খায়েশ থেকে আলাদা কিছু নয়। ইউরোপীয়ান পেনাল কোড যদিও ইউরোপীয়দের অভ্যন্তরীন পরিবেশ পরিস্থিতির স্বার্থে কিংবা উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশগুলোতে (যেমনঃ ওসমানি সামাজ্য আধা উপনিবেশ ছিল) পণ্য রফতানির জন্য বানানো হয়েছিল, তবে এই পেনাল সিস্টেমকে নিছক এক শ্রেনীর দ্বারা অন্য শ্রেনীকে দমন বা আদেশ নিষেধের হুলিয়া জারি করার যন্ত্র হিসেবে দেখা ঠিক হবে না, এমনকি শাসক শ্রেনীর আইনবহির্ভুত সহিংসতা চালানোর ঢাল হিসেবেও দেখা যাবে না। এটিকে বরং দেখতে হবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি হিসেবে যা বৈধতা ও অবৈধতার ফারাক টেনে আইন বানিয়ে সুবিধা আদায় করে।
উপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার পর সমস্ত আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে এটি স্পষ্ট হতে লাগল যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকে সুরক্ষিত না করে একটি দেশের সম্পদের উপর অবিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রন ধরে রাখা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি ও রাজনীতি- অন্তত ইউরোপীয়দের চোখে- আইনি বিষয়ের সাথে একাকার হয়ে যায়। ফলে ইউরোপীয় আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনকে – সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে- বানিজ্যিক আইন ও দন্ডাবিধি উভয়টিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের আহবান করা হয়। অর্থাৎ উপনিবেশগুলোতে সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে আইনের বিষয়ে পরিণত করে ঐ আইন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের হাতে ন্যাস্ত করা হয়। উপনিবেশগুলোতে শাসন পরিচালনার পশ্চিমা এই ব্যবস্থাটি যে মাটি থেকে জন্ম হয়েছে তা থেকে আলাদা কিছু নয়। এ মাটি ইউরোপে চাষ হয়েছে অর্ধ শতাব্দি ধরে। এটাকেই এখন জাতিরাষ্ট্র বলা হয় যা আধুনিক প্রকল্পের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে।
তবে এটি ঠিক যে, আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর সর্মথন ব্যতিরেকে বানিজ্যিক লাভের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার অভীষ্ট লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। এই ব্যবস্থা চাপিয়ে না দিলে উপনিবেশ ও উপনিবেশিত রাজ্যেকে নিয়ন্ত্রন, পরিচালনা ও গঠন করা যেতো না। ঐ ব্যবস্থাটি হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র যা আধুনিক প্রযুক্তিকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পেরেছে। এভাবেই জাতিরাষ্ট্র খুব দ্রুত কলোনিগুলোতে অর্থনৈতিক শোষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকরি প্রক্রিয়া হিসেবে চালু করার জন্য গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠল। যার দরুন জাতিরাষ্ট্রকে এর সকল আইনি হাতিয়ার নিয়ে তাবত দুনিয়ায় রপ্তানি করা হয়।
জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত পুর্বের প্রচলিত রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভেংগে দেয়ার মধ্য দিয়ে (সেটি করা হয়েছে যুদ্ধ চালিয়ে নতুবা অর্থনৈতিক লুন্ঠন চালিয়ে)। দ্বিতীয়ত, উপনিবেশবাদীদের নিজেদের মদদপুষ্ট স্থানীয় বরকন্দাজ ও অভিজাত শ্রেনীকে লুপে নেয়ার মধ্যে দিয়ে। এই অভিজাত শ্রেণিদের সবাই স্রেফ নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে পুর্বের রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিল। এখানে এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতা প্রশ্নে বড়সড় পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ এই অভিজাত শ্রেনী রাষ্ট্রের কেন্দ্রিভুত ক্ষমতার মালিকে পরিণত হয়। ফলে আগেরকার সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতা প্রশ্নে যে চেক এন্ড ব্যলেন্সের পরিবেশ ছিল তা আর ডেভেলপ করার ফুরসত হয়নি। এর ফলে হঠাত করে অধিকাংশ অপ্রতিরোধ্য স্বৈরশাসনের আবির্ভাব ঘটে এবং পিতৃতন্ত্রের অভুতপুর্ব রুপ তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের আইনের ইতিহাসের অধিকাংশ বিস্তৃত সমস্যা জাতিরাষ্ট্রের সুচনাতেই শরিয়াকে মোকাবেলার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেয়। এটা বলা অতিরঞ্জিত হবেনা যে, জাতিরাষ্ট্র ইউরোপে ডেভেলপ হতে পাঁচশ বছর লেগেছে আর তা অপশ্চিমা দেশসমূহে কয়েক দশকের মধ্যেই তাতে পুরাপুরি খাপ খাওয়ানোর দৌড়ঝোপের দরুন অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানত উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে মুসলিম ভুখন্ডে ইসলামি আইন ও জাতিরাষ্ট্রের মাঝে বিরোধের সুত্রপাত ঘটে। ইসলামি আইনের সমস্ত কালনুক্রমকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রাক আধুনিক শরিয়া ব্যবস্থা ও শরিয়া ব্যবস্থাকে বাতিল করে যে ব্যবস্থা আনা হয়েছে তথা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাঝে বিরোধ একবারেই মৌলিক। আলোচনা এগিয়ে নেয়ার পুর্বে সর্তকতামুলক নোক্তা দিয়ে রাখি। এখানে রাষ্ট্রকে সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রিভুত ও সমস্ত অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত কাঠামো বলে যেসব রেফারেন্স হাজির করা হয়েছে সেগুলোকে সরলিকৃত বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কারণ ক্ষমতা সম্পর্কের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রই হচ্ছে প্রতিযোগিতা ও বিরোধমুলক এজেন্ডা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে সন্নিবেশ থাকা। এখানে বুঝতে হবে রাষ্ট্র কোন হাওয়াই মার্কা ছিড়িয়া নয় বরং বিরোধীশক্তি, বিভিন্ন বিভাগ, কর্মী ও জনবল, সংগঠন ও সংস্থা এবং ব্যক্তিদের সম্মিলিত কারখানা মিলিয়েই রাষ্ট্র। যেখানে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের অধীনে থেকে ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে ভাবে এবং নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যার যার কাজকাম বুঝে নেয় ও পালন করে। কোন সন্দেহ নাই তারা একে অপরের বিপরীতে কাজ করলেও পাশাপাশি একসঙে কাজ করে।
রাষ্ট্রের ভিতরে এই যে নানান শক্তির সম্মিলন রয়েছে সেসব শক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আলাদা আলাদা করে পাঠ করা ও সেসবের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা নৃতাত্ত্বিক ও অনান্য সামাজিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের সামগ্রিক আইনি ও বিচারিক কার্যক্রমের মধ্যে ভিন্নতা দেখিয়ে অন্যটার সাথে তুলনা করে আরেকটিকে গুণগতভাবে ভিন্ন ব্যবস্থা বলে সাব্যস্ত করা অকাজের। যাইহোক রাষ্ট্রের শক্তিশালি ও অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা থাকতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র হল এমন এক প্রজাতি যার সদস্যরা বিশেষ উপায়ে আচরন করে, বিশেষ উপায়ে সময় ও দুরত্ব বজায় রাখে, অন্য সকল জীবের মত, বিশেষ উপায়ে লুটের জিনিস ভোগ করে। এটা নিশ্চিত যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই আলাদা। ঠিক যেভাবে প্রতিটি সাপ কিম্বা বাজপাখি আলাদা সৃষ্টি। কিন্তু শাপ এবং বাজ পাখি তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই জীবন যাপন করে। এর মধ্যে কিছু আছে যেগুলা আকৃতি, শক্তি, সামার্থ্য ও আক্রমণ করার কারনে আলাদা। রাষ্ট্র হল বিশেষ ধরনের আধুনিক সৃষ্টি যা শাসন ও কর্তৃত্বের সুসংজ্ঞায়িত কাজগুলিকে (এর মধ্য জনকল্যাণ ও দাতব্য কাজ অন্তর্ভুক্ত) সুন্দরভাবে সম্পাদন করে থাকে। রাষ্ট্রের অঙ্গ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির মাঝে কতটা দ্বন্দ্ব হতে পারে কিম্বা একটি রাষ্ট্র অপরটির থেকে কতটা ভিন্ন তা ধর্তব্যের বিষয় নয়। একটা রাষ্ট্র রাষ্ট্রই ঠিক যেমন বাজপাখি বাজপাখিই, কোন চড়ুই নয়। রাষ্ট্র যেহেতু একটি আইনি প্রতিষ্ঠান তাই রাষ্ট্র ও ইসলামি আইনের মাঝে একটি বিশ্লেষাণত্মক ও কার্যপ্রক্রিয়ামুলক তুলনা করা যথার্থ হতে পারে।
উপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার পর সমস্ত আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে এটি স্পষ্ট হতে লাগলো যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকে সুরক্ষিত না করে একটি দেশের সম্পদের উপর অবিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রন ধরে রাখা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি ও রাজনীতি- অন্তত ইউরোপীয়দের চোখে- আইনি বিষয়ের সাথে একাকার হয়ে যায়। ফলে ইউরোপীয় আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনকে – সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে- বানিজ্যিক আইন ও দন্ডবিধি উভয়টিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের আহবান করা হয়। অর্থাৎ উপনিবেশগুলোতে সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে আইনের বিষয়ে পরিণত করে ঐ আইন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত করা হয়। উপনিবেশগুলোতে শাসন পরিচালনার পশ্চিমা এই ব্যবস্থাটি যে মাটি থেকে জন্ম হয়েছে তা থেকে আলাদা কিছু নয়। এ মাটি ইউরোপে চাষ হয়েছে অর্ধ শতাব্দি ধরে। এটাকেই এখন জাতিরাষ্ট্র বলা হয় যা আধুনিক প্রকল্পের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে।
তবে এটি ঠিক যে, আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর সর্মথন ব্যতিরেকে বানিজ্যিক লাভের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার অভীষ্ট লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। এই ব্যবস্থা চাপিয়ে না দিলে উপনিবেশ ও উপনিবেশিত রাজ্যেকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও গঠন করা যেতো না। ঐ ব্যবস্থাটি হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র যা আধুনিক প্রযুক্তিকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পেরেছে। এভাবেই জাতিরাষ্ট্র খুব দ্রুত কলোনিগুলোতে অর্থনৈতিক শোষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকরি প্রক্রিয়া হিসেবে চালু করার জন্য গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠল। যার দরুন জাতিরাষ্ট্রকে এর সকল আইনি হাতিয়ার নিয়ে তাবত দুনিয়ায় রপ্তানি করা হয়।
জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত পূর্বের প্রচলিত রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভেংগে দেয়ার মধ্য দিয়ে (সেটি করা হয়েছে যুদ্ধ চালিয়ে নতুবা অর্থনৈতিক লুন্ঠন চালিয়ে)। দ্বিতীয়ত, উপনিবেশবাদীদের নিজেদের মদদপুষ্ট স্থানীয় বরকন্দাজ ও অভিজাত শ্রেনীকে লুফে নেয়ার মধ্যে দিয়ে। এই অভিজাত শ্রেণিদের সবাই স্রেফ নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে পূর্বের রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিল। এখানে এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতা প্রশ্নে বড়সড় পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ এই অভিজাত শ্রেনী রাষ্ট্রের কেন্দ্রিভুত ক্ষমতার মালিকে পরিণত হয়। ফলে আগেরকার সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতা প্রশ্নে যে চেক এন্ড ব্যলেন্সের পরিবেশ ছিল তা আর ডেভেলপ করার ফুরসত হয়নি। এর ফলে হঠাৎ করে অধিকাংশ অপ্রতিরোধ্য স্বৈরশাসনের আবির্ভাব ঘটে এবং পিতৃতন্ত্রের অভুতপুর্ব রুপ তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের আইনের ইতিহাসের অধিকাংশ বিস্তৃত সমস্যা জাতিরাষ্ট্রের সুচনাতেই শরিয়াকে মোকাবেলার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেয়। এটা বলা অতিরঞ্জিত হবেনা যে, জাতিরাষ্ট্র ইউরোপে ডেভেলপ হতে পাঁচশত বছর লেগেছে আর তা অপশ্চিমা দেশসমূহে কয়েক দশকের মধ্যেই তাতে পুরাপুরি খাপ খাওয়ানোর দৌড়ঝোপের দরুন অনেক জটিলতা সৃষ্টি করেছে।
চতুর্থত, ইসলামি আইন ও জাতিরাষ্ট দুটি বিপরীত ধারায় পরিচালিত হয়। যেখানে জাতিরাষ্ট্র একচেটিয়া ও চূড়ান্ত কেন্দ্রের দিকে ধাবিত কিংবা বাধ্য সেখানে ইসলামি আইন কেন্দ্রচ্যুত। ইসলামি কাঠামোতে (সামাজিক সংগঠন, শহুরে ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংগঠন, মসজিদ স্থাপত্য ও প্রাক আধুনিক রাজবংশীয় প্রশাসন) বলতে গেলে সমতলভাবে পরিচালিত হয়েছে। বিচারিক নিয়োগের বেলায় তা কেবল নামমাত্র স্তরভিত্তিক ছিলো। বিচার প্রশাসন মুলত নিজস্ব কাঠামোবদ্ধ আইনী পেশায় সীমাবদ্ধ ছিল। যদি স্তরভিত্তিক বলে কিছু থেকে থাকে তবে তা রাজনৈতিক ও সামাজিকতার চেয়ে বরং জ্ঞানগত ও পেশাগত পরিসরে ছিল। ইসলামি আইনের মধ্যে হায়ারার্কি ছিল ব্যাপকভাবে সর্বজনীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাতিরাষ্ট্রের বিদ্যমান বিচারিক ব্যবস্থার হায়ারার্কির মতো নয়, যে হায়ারার্কি শেষমেষ সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিনাদ করে। শরিয়তে এক কাজির রেফারেন্সিয়াল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে আরেক কাজি কিম্বা মুফতি; রাষ্ট্র নয়। জটিল ঘটনাগুলোতে মুফতির বিচারিক সহযোগিদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো এবং আপিলগুলো সাধারনত হায়ার্কির দিকে গড়াতোনা কিন্তু পরবর্তী বিচারকরা সেসব দেখতো ও শুনতো। এমনকি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অফিসে যখন কিছু অভিযোগ দাখিল করা হতো (যেমন অটোমান সাম্রাজ্যে এরকম ঘটনা ঘটেছে) সেগুলা শাসকের মনোযোগ আকর্ষণের স্পষ্ট অভিপ্রায় নিয়েই দেয়া হতো কিংবা করা হতো। এটি ন্যায়বিচারের ব্যক্তিগত রুপ ছিল, কর্পোরেট নয়। বিপরীতে জাতিরাষ্ট্রের বিচারিক ব্যবস্থা বলপূর্বক হায়ারার্কিক্যাল এবং এটি একটি বহিরাগত রাষ্টের হায়ারার্কির জবাবে টিকে থাকে।
পঞ্চমত, আধুনিক রাষ্ট্র নিজেকে বিমুর্ত আইনি সত্তা হিসেবে হাজির করে কিংবা আধুনিক রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলাপে এভাবেই হাজির করা হয়। অর্থাৎ আইন আধুনিক রাষ্ট্রের মতাদর্শিক সুরতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে হাজির হয়েছে। এই মতাদর্শিক সংবিধানের কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক আধিপত্যকে এমনভাবে উপাস্থাপন করা যা পরাধীনতাকে আইনানুগ বা ন্যায়সঙ্গত মনে করে। অর্থাৎ যেটা বলতে হয় সেটা হলো, আধুনিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী সমাজগুলোর স্বাতন্ত্রিকতাকে ধামাচাপা দিয়ে রেখে এর আদর্শিক প্রকল্পকে বাস্তবায়নের চর্চা করে। মার্ক্সীয় ব্যাখানুযায়ী রাষ্ট্র একশ্রেনীর উপর অন্য শ্রেনীর নিয়ন্ত্রণকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে। এই ধামাচাপা দেয়ার কাজটি হল এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। মানুষের উপর প্রথম আদর্শিক শক্তি হিসেবে এটির এমন উপাস্থাপনার মূল এজেন্ডাকে লুকিয়ে রাখে যাতে সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই এজেন্ডাকে বাস্তবায়নের অন্যতম সরঞ্জাম হয়ে উঠে। শরিয়া, এর ফিকহি সংবিধান এবং এর প্রকৃত আর্থ সামাজিক ইতিহাসের আলোকে, না অর্থনৈতিক শ্রেনীকে প্রোমোট করেছে, না পুঁজিবাদ ও শ্রেণির আধিপত্যকে উৎসাহিত করেছে। তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো শরিয়া, এই এজেন্ডার বাইরে এবং বিশেষত কোন শ্রেণির দালালি না করে, দুর্ভেদ্য আদর্শের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তার বিকাশ ঘটায়নি। এই একটি জিনিস, আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পন্ডিতদের হতবুদ্ধ করেছে যা তারা যুতসই বিশ্লেষণ করতে অস্বীকার করে চলছে। অথচ শরিয়াতে এই জিনিস গরহাজির থাকার কারণে আধুনিক অর্থনীতি ও আধুনিক সমাজ বিকাশে ইসলামের ব্যর্থতা বলে ব্যাখা দেয়া হচ্ছে।
ষষ্ঠত, ইসলামি আইন একটি তৃণমুলি ব্যবস্থা। এটি সমাজকে গুরুত্ব দেয় এবং সামাজিক পরিসরে পরিচালিত হয়। এটি বিভিন্ন মাত্রায় ও আকারে, রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার লাগাম টেনে ধরে। ফকিহগন যে সমাজ ও সামাজিক সংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠেন তার আদলেই সমাজকে ঢেলে সাজান এবং আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে আইনের প্রয়োজনীয়তাও একই রকম হয়। ইসলামি আইনের অন্যতম আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হল, মতবাদিক ও বিচারিক ব্যবস্থা হিসেবে, এটি একদম সামাজিক পরিসরে জন্ম লাভ করে এবং সেখানেই এর প্রয়োগ করা হয়। যদিও জাতিরাষ্ট্র গণতান্ত্রিভাবে জনগনের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে তবে জাতিরাষ্ট্রের আইন কেন্দ্রীয় সীমার মধ্যে থেকে চর্চা করা হয়। প্রথমে, রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তিশালি ক্ষমতার রসদ তৈরি করা হয় তারপর তা সামাজিক শৃঙ্খলা গঠন করার জন্য ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা। ইসলামি আইনে সমাজ স্ব-শাসিত। ইসলামি আইনের সাথে নৈতিকতাও জড়িত, যা সমাজের স্বার্থে পরিচালিত হয়। বিপরীতে, জাতিরাষ্ট্রে সমাজ হলো তাই যা উপর থেকে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে শাসিত হয়। পুরুষরা (এখন মহিলারাও) আধুনিক আমলাতন্ত্র পরিচালনা করে এবং কর্পোরেট স্বার্থে আইন বানায়, যে কর্পোরেট সত্তাটাই হলো জাতিরাষ্ট্র। একারণে ম্যক্স ওয়েবার ও সাইয়েদ কুতুব বলেন জাতিরাষ্ট্র মানুষের উপর মানুষের শাসনের চেয়ে বরং আরো বাড়তি কিছু। এরমানে এখানে এইটা বলা হচ্ছে না যে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র যাদেরকে শাসন করে তাদেরকে উপেক্ষা করে ক্ষমতার বিকাশ ও চর্চা করছে বরং আলাপটা হলো এটি পরিশালীত কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে জাতীয় নাগরিকদের একীভূত করেছে। তাদেরকে নতুন মতার্দশিক রুপে আকার দিয়েছে। সর্বোপরি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ামবালীর ছকে নিজদের সমর্পন করতে বাধ্য করেছে।
সপ্তমত, ইসলামি আইন ও জাতি রাষ্ট্র-বিরোধ মিমাংসা ও সমাজ গঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্য লালন করলেও, তাদের কাজের প্রভাব কিন্তু সমাজে ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়েছে। জাতি রাষ্ট্রের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থা ও নাগরিকদেরকে নিজস্ব সিস্টেমের অধীনে নিয়ে এসে সমজাতীয়করণ করে ফেলা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এটি নজরদারি, শৃঙ্খলার বিধান ও শাস্তির ব্যবস্থাকে বহাল রাখে। জাতি রাষ্ট্রের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সাজানো হয় সুনাগরিক উৎপাদন করার জন্য -যারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, শৃঙ্খলা ও বিধানের প্রতি অনুগত থাকে, কঠোর পরিশ্রমি ও অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ শাস্তি আধুনিক রাষ্ট্রের অভিন্ন ও একক বৈশিষ্ট্য। এর ফলাফল হলো এমন সুনাগরিক জন্ম দেয়া যারা রাষ্ট্রের তাবেদারি করে। আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে। আইন, শাস্তি ও নজরদারির সরঞ্জাম ছাড়া কোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারেনা। রাষ্ট্রের ধারণায় ও সংজ্ঞায় সহিংসতার চর্চার একমাত্র অধিকার রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। আমার সচেতন জানাশোনায় মানব ইতিহাসে আধুনিক রাষ্ট্রই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা নিজেকে সহিংসতা চর্চার একমাত্র হক্কদার দাবি করে বসেছে। নাগরিকরা এসব মেনে নিয়েছে অথবা মেনে নেয়ার জন্য শর্তারোপ করা হয়েছে। আইনি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শ ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে অনুগত নাগরিক বানানোর প্রজেক্ট রাষ্ট্রের সফলতার পেছনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করেছে। অপরদিকে ইসলামি আইন কখনো জাতীয় নাগরিক তৈরি নিয়ে মাথা ঘামায়না। এমনকি অন্য কোনো ধরনের নাগরিক নিয়েও না। এটি আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে ধারণা করেনা। এটি সহিংসতার একচ্ছত্র অধিকারও দাবি করেনা। আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনায় কখনো সমাজ ও ব্যাক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবস্থায় অধীনস্ত করার চেষ্টা ইসলামি শরিয়া করে নাই।